মুসলিম বিশ্বের শক্তি, ঐক্য ও গৌরবের কথা বলতে গেলে অনেকের চোখে প্রথম ভেসে ওঠে মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলোর নাম। একসময় এখান থেকেই ইসলামের বাণী বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল, জন্ম নিয়েছিল বীরত্ব, জ্ঞান ও সভ্যতার অসংখ্য অধ্যায়। কিন্তু সেই ইতিহাস আজ অতীতের পাতা। আরব রাষ্ট্রগুলোর বড় অংশ এখন নিজস্ব ঐতিহ্য ও মর্যাদা ভুলে পশ্চিমা শক্তির ছায়াতলে নত হয়ে আছে।
এই পতনের শেকড় খুঁজে পাওয়া যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় থেকে। ওসমানি সাম্রাজ্যের পতনের পর যে আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্ম হয়েছিল, তার পেছনে মূল চালিকা শক্তি ছিল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থরক্ষা। সেই রাষ্ট্রগুলো জনগণের ইচ্ছা বা স্বাধীনতার স্বপ্ন পূরণের জন্য তৈরি হয়নি, বরং উপনিবেশিক শক্তির আধিপত্য বজায় রাখার জন্যই তাদের গড়া।
ব্রিটিশ পরিকল্পনা ও ‘আরব মুখোশ’-এর জন্ম
১৯১৮ সালে ওসমানি শাসনের পতনের পর মধ্যপ্রাচ্যে ব্রিটিশ প্রভাব দ্রুত দৃশ্যমান হয়। ব্রিটিশ ভারতের এক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তখন স্বীকার করেছিলেন- পুরোনো নীতি আর কার্যকর নয়; নতুন লক্ষ্য পূরণে নতুন পথ নিতে হবে। তার ভাষায়, এর জন্য দরকার ‘আরব মুখোশ’, যা আগের পরিকল্পনার তুলনায় অনেক বেশি মজবুত হবে এবং দীর্ঘস্থায়ীভাবে ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করবে।
১৯১৯ সালের প্যারিস শান্তি সম্মেলনের সময় ব্রিটিশরা বুঝে গেল যে, ‘স্বনির্ধারণের’ নতুন আন্তর্জাতিক আবহে সরাসরি শাসন চাপিয়ে দেওয়া আর সম্ভব হবে না। তাই তারা পরিকল্পনা করল এমন এক শাসন কাঠামো, যা বাইরে থেকে ‘স্থানীয় কর্তৃত্ব’ মনে হলেও আসলে থাকবে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে।
প্রতিশ্রুতির আড়ালে প্রতারণা
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হয়ে কাজ করা অনেক কর্মকর্তা, যেমন টি ই লরেন্স বিশ্বাস করতেন যে, তারা আরবদের স্বাধীনতা অর্জনে সাহায্য করছেন। কিন্তু বাস্তবে তাদের ভূমিকা ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করা। একদিকে আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখা, অন্যদিকে ‘নতুন স্বাধীনতা’ প্রদানের ভান করা।
এই ‘আরব মুখোশ’ ছিল আসলে ‘পরোক্ষ শাসন’-এর নতুন সংস্করণ, যা ব্রিটিশরা আগেই আফ্রিকায় ব্যবহার করেছিল। মূল উদ্দেশ্য ছিল, যে কোনো প্রকৃত স্বাধীনতার উদ্যোগ দমন করে স্থানীয়দের হাতে শাসনের ভার দেওয়া, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখা নিজেদের হাতে।
সাইক্স-পিকো ও বেলফোর : মুখোশের ভিত মজবুত করা
১৯১৬ সালে ব্রিটিশরা ওসমানিদের বিরুদ্ধে হাশেমি নেতা শরিফ হোসাইন ইবনে আলিকে সমর্থন দেয় এবং আরব বিদ্রোহে উসকে তোলে। তাদের প্রতিশ্রুতি ছিল ফিলিস্তিনসহ বৃহৎ একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। কিন্তু গোপনে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা সাইক্স-পিকো চুক্তির মাধ্যমে আরব ভূখণ্ড নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেছিল যা সেই প্রতিশ্রুতির সম্পূর্ণ বিপরীত।
১৯১৭ সালে আসে বেলফোর ঘোষণা- ফিলিস্তিনে একটি ‘ইহুদি জাতীয় আবাস’ গঠনের পক্ষে ব্রিটিশ সমর্থন। সে সময় ইহুদিরা ছিল সংখ্যালঘু, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ আরবদের অধিকারকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ঘোষণায় তাদের ‘ইহুদিবহির্ভূত সম্প্রদায়’ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।
ক্ষুব্ধ আরবদের শান্ত করার কৌশল
সাইক্স-পিকো ও বেলফোর ঘোষণার খবর ফাঁস হলে আরব বিশ্বে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্ষোভ প্রশমিত করতে ব্রিটিশ ও ফরাসিরা ১৯১৮ সালের নভেম্বরে ঘোষণা দেয়- তাদের লক্ষ্য হলো তুর্কি নিপীড়ন শেষ করে স্থানীয়দের স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা। কিন্তু বাস্তবে উদ্দেশ্য ছিল নতুন মুখোশটিকে আরও দৃঢ় করা।
এই নতুন কাঠামোতে শাসক হতে হতো এমন একজন, যিনি ব্রিটিশ স্বার্থে অনুগত থাকবেন, ইহুদি বসতি স্থাপনে বাধা দেবেন না এবং ফিলিস্তিন মুক্তির দাবিতে জনরোষ দমন করবেন। এতে মিলত কেবল নামমাত্র স্বাধীনতা। হাশেমি পরিবার যেমন এই কাঠামোতে মানিয়ে নেয়, তেমনি মানিয়ে নেয় ইবনে সউদ ও মিসরের বাদশাহ ফুয়াদ। শরিফ হোসাইনের দুই ছেলে ফয়সাল ও আবদুল্লাহকে যথাক্রমে ইরাক ও ট্রান্সজর্ডানে পুতুলশাসক হিসেবে বসানো হয়।
আরব-মার্কিন লেখক আমিন রিহানি মন্তব্য করেছিলেন- এ ধরনের শাসকরা উপনিবেশবাদের ক্রীড়ানক থেকেও বেশি, কিন্তু স্বাধীন নেতা থেকে কম। এর বিপরীতে তুরস্কের আতাতুর্ক পশ্চিমা বিভাজনের বিরুদ্ধে সফল প্রতিরোধ গড়ে তুললেও, আরব রাষ্ট্রগুলো তেমন দৃঢ় সার্বভৌমত্ব অর্জন করতে পারেনি।
নাকবা ও দ্বিতীয় ঢেউয়ের প্রতিরোধ
১৯৪৮ সালের নাকবা বা ফিলিস্তিনিদের গণউচ্ছেদের পর অনেক আরব সামরিক কর্মকর্তা পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। মিসরে গামাল আবদেল নাসের ১৯৫২ সালে ব্রিটিশপন্থি রাজাকে উৎখাত করে বিপ্লব ঘটান। ইরাকে ১৯৫৮ সালে পতন হয় হাশেমি রাজতন্ত্রের।
তবে ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে পরাজয়ের পর যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটিশদের জায়গা নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে প্রধান নিয়ন্ত্রক শক্তি হয়ে ওঠে এবং নতুনরূপে আরব মুখোশ পুনর্গঠন করে।
‘আরব মুখোশ ২.০’: আমেরিকান সংস্করণ
দ্বিতীয় প্রজন্মের এই মুখোশের মূল নকশা ব্রিটিশ আমলের মতোই, তবে এবার যুক্ত হয়েছে তেলের অর্থ পশ্চিমে পুনর্বিনিয়োগের শর্ত। বর্তমান আরব শাসকরা অনেক সময় নিজেদের কিছুটা স্বাধীনতার ভান দেন, কিন্তু বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে, বিশেষত ফিলিস্তিন প্রশ্নে, তারা জনগণের বিপরীতে অবস্থান নেন।
মার্কিন কৌশলে ইসরায়েলকে মধ্যপ্রাচ্যের আধিপত্যের কেন্দ্রবিন্দু করা হয়েছে। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি, অসলো চুক্তি, এমনকি সাম্প্রতিক আব্রাহাম চুক্তি সবই মূলত আত্মসমর্পণের সমঝোতা। এসবের আড়ালে আরবরা একের পর এক ছাড় দিয়েছে, আর ইসরায়েল দখল বিস্তৃত করেছে।
গাজা, লেবানন ও ইয়েমেন : ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠা
আজও গাজা, লেবানন ও ইয়েমেনে প্রতিরোধ অব্যাহত আছে। এই প্রতিরোধই দেখিয়ে দিচ্ছে, সব আরব নেতা পশ্চিমা আধিপত্যের মুখোশ পরে নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রঘনিষ্ঠ আরব শাসকরা এই প্রতিরোধকে উপেক্ষা করেন, দমন করেন বা দুর্বল করে দেন। কেউ কেউ ইসরায়েলি দখলদারিত্বে বিনিয়োগ করতেও দ্বিধা করেন না।
মুখোশের আয়ু কত দিন?
আজ আরব জাতীয়তাবাদ প্রায় বিলুপ্ত, কিন্তু ‘আরব মুখোশ’ এখনো অটুট। ইতিহাস স্পষ্ট করে বলছে- এই মুখোশ কখনো জনগণের মুক্তি আনে না; বরং মুক্তির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু উপনিবেশবাদ যেমন শেষ হয়েছে, এই মুখোশও চিরকাল টিকবে না।
গাজায় চলমান গণহত্যা, ইসরায়েলি দখলদারিত্ব এবং পশ্চিমা দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে জনমনে জমতে থাকা ক্ষোভ হয়তো একদিন এই মুখোশ ছিঁড়ে ফেলবে। তখনই বোঝা যাবে- আরবদের মুখোশ টিকিয়ে রাখার সময় ফুরিয়েছে, নাকি তারা আবারও ইতিহাসের সেই গৌরবময় পথে ফিরতে পারবে। (মিডল ইস্ট আই থেকে অনুদিত)
উসামা মাকদিসি : ইতিহাসবিদ এবং ‘চ্যান্সেলরস চেয়ার’, ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়
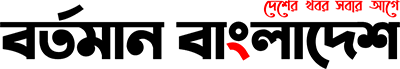






































আপনার মতামত লিখুন :